সাইবার বুলিং: নারীর রাজনৈতিক অগ্রযাত্রায় অন্তরায়
মনজিলা ঝুমা : বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের সমাজব্যবস্থা এখনো একটি পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা দ্বারা প্রভাবিত। যদিও নারীরা আজ রাজনীতি, প্রশাসন, আইন, শিক্ষা, ব্যবসা—সব ক্ষেত্রে নিজেদের সক্ষমতা প্রমাণ করেছেন, তবুও প্রতিনিয়ত তাদের সামনে সৃষ্টি করা হয় এক অদৃশ্য দেয়াল। নারীর পথরোধ করার দেয়ালগুলো দৃশ্যমান নয়, তবে তার অস্তিত্ব তীব্রভাবে অনুভব করা যায়। এই দেয়ালের নাম কখনো হয় সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, কখনো পারিবারিক দায়বদ্ধতা, আবার কখনো বা সাইবার বুলিং—যা আসলে পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য (domination) প্রতিষ্ঠার এক সূক্ষ্ম কিন্তু সুপরিকল্পিত কৌশলমাত্র।
বিশেষ করে রাজনীতি নামক ক্ষমতাকেন্দ্রিক ও পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত অঙ্গনে নারীর প্রবেশ অনেকের কাছেই অগ্রহণযোগ্য ও ভয়ংকর এক হুমকি বলে মনে হয়। কারণ, রাজনীতি মানেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, নেতৃত্বের জায়গা, এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রভাব বিস্তারের সুযোগ—আর ঠিক এখানেই নারীর ভূমিকা সীমিত করে দেওয়ার প্রয়াস চলে নানা ছলচাতুরী ও কাঠামোগত নিপীড়নের মাধ্যমে।
সমাজ ও পরিবার মিলে নারীর জন্য তৈরি করে দেয় এক ধরনের ‘সামাজিকভাবে স্বীকৃত সীমা’ বা লিমিট—যার বাইরে গিয়ে নেতৃত্ব দেওয়া, মত প্রকাশ করা, কিংবা জনমত গঠন করা যেন তাদের জন্য বারণ। নারীর আদর্শ পরিচিতি যেন একজন ‘অনুসারী’, ‘সহযোগী’, কিংবা ‘পিছনের সারির নির্ভরযোগ্য জনবল’—নেতৃত্বের আসনে তার অবস্থান অনেকের দৃষ্টিতে নিয়মভঙ্গ বা বিদ্রোহের সামিল।
আর যে নারী সাহস করে এই সীমারেখা অতিক্রম করেন, নিজের পরিচয় ও অবস্থান নিজেই গড়ে তুলতে চান, রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে চান—তাকে ঠেকাতে শুরু হয় নতুন ধরনের নিপীড়ন। এই নিপীড়ন আর শারীরিক নয়, বরং অনেক বেশি চতুর এবং ধ্বংসাত্মক—এটি ভার্চ্যুয়াল প্ল্যাটফর্মে ঘটে, যার নাম ‘সাইবার বুলিং’।
সোশ্যাল মিডিয়াকে হাতিয়ার বানিয়ে এই নারী নেতৃত্বকে দুর্বল করার এক নীরব যুদ্ধ চলে। কুৎসা রটানো, চরিত্রহনন, অপমানসূচক মন্তব্য, এমনকি যৌন হয়রানিমূলক বার্তা ও ছবি ছড়িয়ে দেওয়া—সবই এর অংশ। উদ্দেশ্য একটাই: নারীর আত্মবিশ্বাস ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতাকে ধ্বংস করা, তাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলা, এবং তাকে চুপ করিয়ে দেওয়া।
এই সাইবার সহিংসতা নিছক একক অপরাধ নয়—এটি বৃহৎ পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার, যার মাধ্যমে নারীকে রাজনীতির কেন্দ্র থেকে সরিয়ে রাখা হয়।
এই বাস্তবতাকে স্বীকার করে, আমরা যদি প্রতিরোধ না গড়ি—তবে ‘রাজনীতিতে নারীর সমান অংশগ্রহণ’ কেবল একটি শ্লোগান হয়েই থাকবে, বাস্তবতা নয়। তাই সময় এসেছে, এই দেয়ালগুলিকে চিহ্নিত করে, ভেঙে ফেলার। কারণ, একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক ও ন্যায্য রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হলে—নারীকে নেতৃত্বের আসনে দেখতে হবে, এবং সেই পথকে করতে হবে নিরাপদ, সম্মানজনক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক।
বিশেষ করে রাজনীতি নামক ক্ষমতাকেন্দ্রিক ও পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত অঙ্গনে নারীর প্রবেশ অনেকের কাছেই অগ্রহণযোগ্য ও ভয়ংকর এক হুমকি বলে মনে হয়। কারণ, রাজনীতি মানেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, নেতৃত্বের জায়গা, এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রভাব বিস্তারের সুযোগ—আর ঠিক এখানেই নারীর ভূমিকা সীমিত করে দেওয়ার প্রয়াস চলে নানা ছলচাতুরী ও কাঠামোগত নিপীড়নের মাধ্যমে।
সমাজ ও পরিবার মিলে নারীর জন্য তৈরি করে দেয় এক ধরনের ‘সামাজিকভাবে স্বীকৃত সীমা’ বা লিমিট—যার বাইরে গিয়ে নেতৃত্ব দেওয়া, মত প্রকাশ করা, কিংবা জনমত গঠন করা যেন তাদের জন্য বারণ। নারীর আদর্শ পরিচিতি যেন একজন ‘অনুসারী’, ‘সহযোগী’, কিংবা ‘পিছনের সারির নির্ভরযোগ্য জনবল’—নেতৃত্বের আসনে তার অবস্থান অনেকের দৃষ্টিতে নিয়মভঙ্গ বা বিদ্রোহের সামিল।
আর যে নারী সাহস করে এই সীমারেখা অতিক্রম করেন, নিজের পরিচয় ও অবস্থান নিজেই গড়ে তুলতে চান, রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে চান—তাকে ঠেকাতে শুরু হয় নতুন ধরনের নিপীড়ন। এই নিপীড়ন আর শারীরিক নয়, বরং অনেক বেশি চতুর এবং ধ্বংসাত্মক—এটি ভার্চ্যুয়াল প্ল্যাটফর্মে ঘটে, যার নাম ‘সাইবার বুলিং’।
সোশ্যাল মিডিয়াকে হাতিয়ার বানিয়ে এই নারী নেতৃত্বকে দুর্বল করার এক নীরব যুদ্ধ চলে। কুৎসা রটানো, চরিত্রহনন, অপমানসূচক মন্তব্য, এমনকি যৌন হয়রানিমূলক বার্তা ও ছবি ছড়িয়ে দেওয়া—সবই এর অংশ। উদ্দেশ্য একটাই: নারীর আত্মবিশ্বাস ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতাকে ধ্বংস করা, তাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলা, এবং তাকে চুপ করিয়ে দেওয়া।
এই সাইবার সহিংসতা নিছক একক অপরাধ নয়—এটি বৃহৎ পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার, যার মাধ্যমে নারীকে রাজনীতির কেন্দ্র থেকে সরিয়ে রাখা হয়।
এই বাস্তবতাকে স্বীকার করে, আমরা যদি প্রতিরোধ না গড়ি—তবে ‘রাজনীতিতে নারীর সমান অংশগ্রহণ’ কেবল একটি শ্লোগান হয়েই থাকবে, বাস্তবতা নয়। তাই সময় এসেছে, এই দেয়ালগুলিকে চিহ্নিত করে, ভেঙে ফেলার। কারণ, একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক ও ন্যায্য রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হলে—নারীকে নেতৃত্বের আসনে দেখতে হবে, এবং সেই পথকে করতে হবে নিরাপদ, সম্মানজনক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক।
সাইবার বুলিংয়ের মাধ্যমে নারীর ব্যক্তিত্বকে ভেঙে ফেলা, আত্মবিশ্বাস হরণ করা এবং সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়। যেমন—
- রাজনৈতিকভাবে সচেতন কোনো নারী যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় মত প্রকাশ করেন, তখন তার পোশাক, ব্যক্তিজীবন, বা পারিবারিক পরিচয় নিয়ে কটাক্ষ করা হয়।
- কখনো তার ছবি এডিট করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, চরিত্র হননের চক্রান্ত চলে।
- কখনো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগ তুলে তাকে ‘টার্গেট’ করা হয়।
- তার কণ্ঠকে থামাতে ভয়ভীতি প্রদর্শন, হুমকি, এমনকি হত্যার ইঙ্গিতও দেওয়া হয়।
এসব কর্মকাণ্ড মূলত নারীর ওপর আধিপত্য বজায় রাখার হাতিয়ার। এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক খেলা, যার মাধ্যমে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা বার্তা দেয়: “এই জায়গাটি তোমার জন্য নয়”। ফলে অনেক প্রতিভাবান, সচেতন নারী রাজনীতির মাঠ থেকে পিছিয়ে আসেন। এটি কেবল একজন নারীর ক্ষতি নয়, বরং পুরো সমাজের জন্য ক্ষতিকর— কারণ এতে নেতৃত্বের বৈচিত্র্য নষ্ট হয়, নারীর দৃষ্টিভঙ্গি রাজনীতিতে উপেক্ষিত থাকে।
অবস্থার পরিবর্তনে কী করণীয়?
১. আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করা: সাইবার বুলিংয়ের বিরুদ্ধে শক্ত আইন থাকলেও, বাস্তবায়ন দুর্বল। দ্রুত বিচার ও অপরাধীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রয়োজন।
২. রাজনৈতিক দলগুলোর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন: নারীদের শুধুই ‘প্রতীকী’ অংশগ্রহণ না দিয়ে, প্রকৃত নেতৃত্বে আনার মনোভাব গড়ে তুলতে হবে।
৩. সাইবার জগতে নারীর সম্মান রক্ষা: অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোতে হেট স্পিচ এবং যৌন হয়রানি মোকাবেলায় আরও কঠোর নীতিমালা প্রয়োজন।
৪. নারীর আত্মবিশ্বাস ও প্রশিক্ষণ: নারীদের প্রযুক্তিগত সচেতনতা, ডিজিটাল নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষা কৌশল শেখানো প্রয়োজন।
৫. সমাজের মানসিকতা বদল: নারীকে নেতৃত্ব দিতে দেখার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে পরিবার ও শিক্ষাব্যবস্থায়।
উপসংহার
সাইবার বুলিং কেবল প্রযুক্তিগত অপরাধ নয়— এটি রাজনৈতিক আধিপত্যের এক সূক্ষ্ম, কিন্তু ভয়ঙ্কর অস্ত্র। এটি এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নারীর কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, তাকে নেতৃত্বের স্থান থেকে দূরে সরিয়ে রাখার অপচেষ্টা চলে। যখন একজন নারী তার মত প্রকাশ করেন, নেতৃত্বে আসার সাহস দেখান, বা সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থাকে প্রশ্ন করেন—তখনই এই সাইবার বুলিং নামক ভার্চুয়াল নিপীড়ন শুরু হয়।
এই নিপীড়ন কেবল মানসিকভাবে আঘাত হানে না, বরং তার রাজনৈতিক অবস্থান, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা এবং ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের পথকেই বিপন্ন করে তোলে। ফলে নারীর কণ্ঠ ক্রমাগত দুর্বল হয়ে পড়ে, এবং রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ একটি অলীক কল্পনা হয়ে দাঁড়ায়।
যদি এই বাস্তবতাকে আমরা বুঝে প্রতিহত করতে না পারি—তবে ‘রাজনীতিতে নারীর সমতা ও অন্তর্ভুক্তি’ কেবল নীতিনির্ধারকের মুখের বুলি কিংবা রাষ্ট্রীয় কাগজপত্রের নীতিমালায় সীমাবদ্ধ থাকবে। বাস্তবে তার প্রতিফলন ঘটবে না।
তাই এখনই সময়, নারীদের আর নয় নিরব দর্শক হিসেবে দেখার; এখন তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কেন্দ্রবিন্দুতে আনতে হবে। রাজনীতি, প্রশাসন, আইন প্রণয়ন—সব জায়গায় নারীকে নেতৃত্ব দিতে দিতে হবে পূর্ণাঙ্গ সুযোগ ও মর্যাদা। কেবলমাত্র তখনই একটি সমাজ সত্যিকার অর্থে সাম্যের, সম্মানের ও ন্যায়বিচারের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠতে পারে।
সাইবার সহিংসতা রুখে দিয়ে, নারীর কণ্ঠকে সুর দেওয়ার মাধ্যমেই আমরা গড়তে পারি এমন একটি রাষ্ট্র—যেখানে নেতৃত্ব মানে শুধু পুরুষের একচ্ছত্র আধিপত্য নয়, বরং নারীর সমান অংশীদারিত্বও।
লেখক : আইনজীবী, কেন্দ্রীয় সংগঠক(দক্ষিনাঞ্চল), জাতীয় নাগরিক পার্টি ও সদস্য খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ।
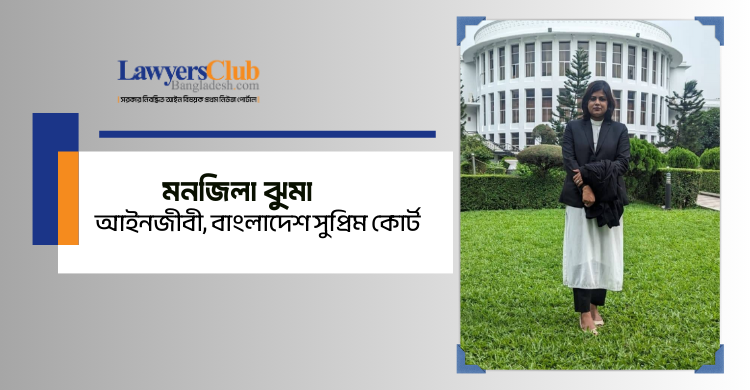
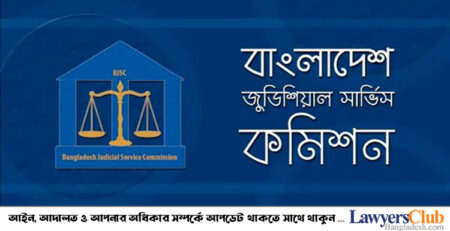

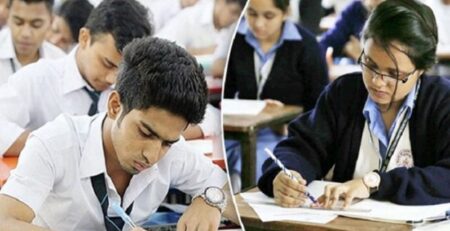

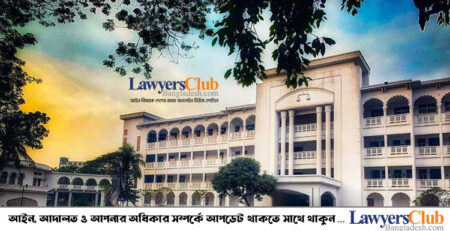

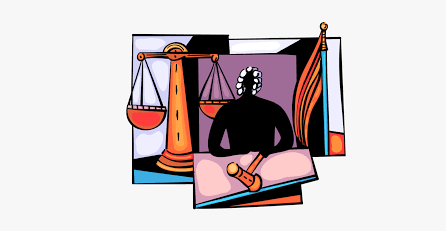


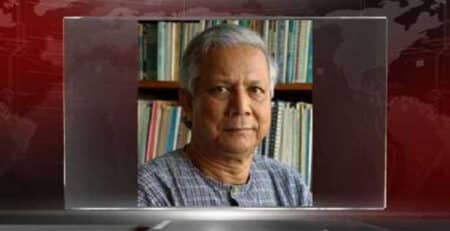
Leave a Reply