মেধাভিত্তিক সরকারি আইন কর্মকর্তা নিয়োগে স্বাধীন প্রসিকিউশন সার্ভিস কমিশন জরুরি
নোমান আলম: আমাদের দেশের ফৌজদারী বিচারব্যবস্থা হলো অ্যাডভারসারিয়াল বা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় বিচারক রেফারি’র ভূমিকায় থাকে। বাদী ও বিবাদীর আইনজীবীরা মামলার বিচার্য বিষয় তুলে ধরেন। বিচারকের কাজ আইন ও আদালতে পেশকৃত তথ্যাদির আলোকে রায় দেয়া। এখানে প্রমাণের মানদণ্ড কঠোর।
আইনের মূলনীতি অনুযায়ী আসামিকে নির্দোষ গণ্য করে বিচার শুরু হয়। এখানে বাদীকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে হয় যে আসামি দোষী। কমন ল’ ব্যবস্থায় তাই আসামিকে দোষী প্রমাণ করা অত্যন্ত কঠিন। অন্যদিকে সিভিল ল’ ব্যবস্থায় ইনকুইজিটোরিয়াল বা অনুসন্ধানমূলক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এই ব্যবস্থায় আদালতের কাজ হলো সত্য বের করা। তাই আদালত বাদী, বিবাদী ও সাক্ষীদের জেরা করতে পারেন। এখানে অভিযুক্তকে প্রমাণ করতে হয় যে সে নির্দোষ।
আমাদের দেশে যেহেতু কমন ল’ ব্যবস্থা বিদ্যমান এখানে একটা ফৌজদারী মামলার পরিণতি আইনজীবীর উপর নির্ভর করে অনেকটা। বাদী বা আসামীপক্ষের আইনজীবী তার দক্ষতা এবং আইনি প্রজ্ঞা দিয়ে তার মক্কেলকে জিতিয়ে আনতে পারেন। এক্ষেত্রে কোন একটি পক্ষের আইনজীবী যদি তুলনামূলক অধিক দুর্বল হয় তাহলে দেখা যাবে মক্কেল ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হবে।
ফৌজদারি অপরাধ হল মূলত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই কৃত অপরাধ। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ফৌজদারি মামলার বাদী- রাষ্ট্র। এজাহারে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের কোন কর্মচারী বাদী না হলেও ফৌজদারি মামলার পক্ষ হল রাষ্ট্রই। রাষ্ট্রের পক্ষ্যে কোন বাদী আদালতে সাক্ষ্য় দিয়ে থাকে। যাকে সংবাদদাতা বলা হয়। ফৌজদারি মামলায় সরকার একটি পক্ষ ও আসামীরা অন্য একটি পক্ষের হয়ে থাকে। উচ্চতর আদালতে ফৌজদারি মামলার নামকরণও এমনই হয়ে থাকে।
রাষ্ট্রের পক্ষে যেসব আইনজীবী ফৌজদারী মামলা পরিচালনা করেন তারা হলেন পাবলিক প্রসিকিউটর বা পিপি।
আরও পড়ুন: নারীর গর্ভপাত বনাম অনাগত শিশুর জীবনের অধিকার
ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৯২ ধারায় সরকারকে পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগ করার ক্ষমতা দিয়েছে। সরকার কোন স্থানীয় এলাকায় সাধারণভাবে বা কোন মামলায় বা কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর মামলার জন্য পাবলিক প্রসিকিউটর নামক এক বা একাধিক অফিসার নিয়োগ করতে পারেন। পাবলিক প্রসিকিউটরের অনুপস্থিতিতে বা যেক্ষেত্রে পাবলিক প্রসিকিউটর নিযুক্ত হন নাই সেক্ষেত্রে মামলা পরিচালনার জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সরকার কর্তৃক এ সম্পর্কে নির্ধারিত পদের পুলিশ অফিসার ব্যতীত অন্য যে কোন ব্যক্তিকে পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগ করতে পারবেন।
এছাড়া ১৯৬০ সালের লিগ্যাল রিমেম্বারেন্সারস ম্যানুয়েল (এল,আর,ম্যানুয়েল) এ কিভাবে পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগ করা হবে,পাবলিক প্রসিকিউটরের যোগ্যতা,বয়স সীমা,মেয়াদ,ছুটি ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ আছে। পাবলিক প্রসিসিউটর নিয়োগের জন্য পাঁচ বছরের আইনজীবি হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে,বয়স ৬০ বছরের কম হতে হবে এবং নিয়োগ তিন বছরের জন্য হবে।
বাস্তবতা বিবেচনা করলে দেখা যায় আমাদের দেশে যুগে যুগে পাবলিক প্রসিকিউটর নিযুক্ত হয়েছে রাজনৈতিক বিবেচনায়। রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ মানেই যে এরা অদক্ষ,অযোগ্য সেটা নয়। কিন্তু যখন রাজনীতিই একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হয়ে উঠে তখন সেখানে অদক্ষ,অযোগ্য কেউ ঢুকে যাওয়ার অবারিত সুযোগ সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের আইন অঙ্গনে যারা প্রথিতযশা আইনজীবি আছে এদের অনেকেই মূলধারার রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই রাজনৈতিক বিবেচনা যে সব সময় খারাপ কিছু বয়ে আনবে সেটাও সঠিক নয়।
কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে দেখা যায় বর্তমানে যাদের পিপি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় এরা সংশ্লিষ্ট বারে দক্ষ আইনজীবি হিসেবে পরিচিত না। যেহেতু রাষ্ট্র মামলা পরিচালনা করে, রাষ্ট্রীয় আইনজীবি যদি অদক্ষ,অযোগ্য হয় সেখানে ভিকটিম ক্ষতিগ্রস্থ হবে তথা ন্যায়বিচার ভূলণ্ঠিত হবে।
আরও পড়ুন: বিচার ব্যবস্থা সংস্কারে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার যা হতে পারে
একটি ফৌজদারী মামলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্ব হলো ট্রায়াল স্টেজ। যারা আইনপেশায় আছে বা আদালত সংশ্লিষ্টতা আছে এরা জানে ট্রায়াল লয়্যার প্রত্যেক আদালতে আছে তুলনামূলক কম। সাক্ষ্য,জেরা,যুক্তিতর্ক এই বিষয়গুলোতে অনেক আইনী জ্ঞান, টেকনিক্যাল জ্ঞান, অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে। যেটা ফুলটাইম রাজনীতি করা একজন আইনজীবির পক্ষে থাকা স্বাভাবিকভাবে সম্ভব নয়। অনেক স্পর্শকাতর মামলায় আসামীপক্ষে থাকে ব্যক্তিগতভাবে নিযুক্ত আইনজীবি। যাদের সামনে আদালতে দেখা যায় সরকারী আইন কর্মকর্তা এক প্রকার অসহায়।
রাজনৈতিকভাবে নিয়োগ হওয়ায় অনেকে নিজেদের পদকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের চেয়ে দলীয় পুরষ্কার হিসেবে বেশী বিবেচনা করে। তাই রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের চেয়ে দলীয় দায়িত্ব পালনকেই এরা অধিক গুরুত্ব দেয়। পিপিদের সিন বাণিজ্যের কথা আদালতের ওপেন সিক্রেট।
এছাড়া পাবলিক প্রসিকিউটরদের যে মামলার খরচ আর সম্মানী দেয়া হয় তা বাস্তবতা বিবেচনায় অপ্রতুল। কাজেই তারা রাষ্ট্রীয় এই দায়িত্ব পালনে সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হন। এই সীমাবদ্ধতা থেকে কেউ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন থেকে বিরত থাকে, কেউ পদকে অবৈধ কাজে ব্যবহার করে।
বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোগুলোর যে ইতিবাচক সংস্কার শুরু হয়েছে সেখানে পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগ,নিয়ন্ত্রণ, তদারকি’র জন্য আলাদা কমিশন গঠন করা জরুরী। জুডিশিয়াল অফিসার নিয়োগের জন্য যেমন স্বতন্ত্র জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন আছে তেমনই প্রসিকিউশন সার্ভিস কমিশন বা অন্য যেকোন নামে একটা স্বাধীন কমিশন গড়ে তুলতে হবে। অনেকে বলছেন জুডিশিয়াল সার্ভিসের পরীক্ষার্থীদের থেকে পিপি নিয়োগ দিতে। এক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ আছে।
শুধুমাত্র আইনি জ্ঞান ভালো আইনজীবী হওয়ার জন্য যথেষ্ট না। এখানে অভিজ্ঞতা এবং কোর্টের প্রেক্টিক্যাল অনেক জ্ঞান জরুরী। কাজেই গবেষণার মাধ্যমে এবং অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে বের করতে হবে কোন প্রক্রিয়ায় কাদেরকে পরীক্ষার মাধ্যমে পিপি বানালে আদালতের কার্যক্রম গতি পাবে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। এক্ষেত্রে যথাযথ প্রশিক্ষণ, ভালো সম্মানী এবং তদারকি অত্যন্ত জরুরী।
লেখক: শিক্ষানবিশ আইনজীবী, জেলা ও দায়রা জজ আদালত, চট্টগ্রাম।


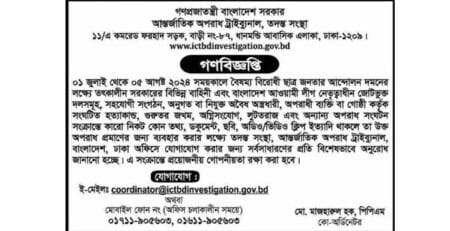



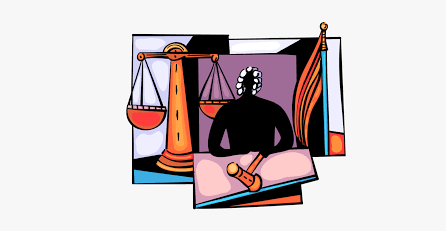

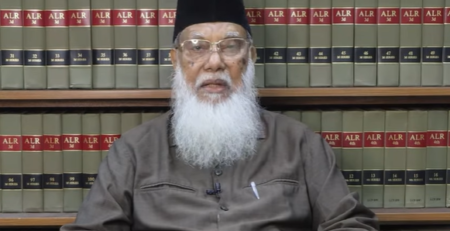


Leave a Reply