আইন শিক্ষা ও আইন পেশার সেতুবন্ধনে প্রতিবন্ধকতা: একটি পর্যালোচনা
সাঈদ আহসান খালিদ: বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের শিক্ষকবৃন্দ আইন বিষয়ে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর অনেকে আইনের স্পেশালাইজড ফিল্ডে দেশে বা বিদেশে উচ্চশিক্ষা এবং পিএইচডি অর্জন করেন। পরবর্তীতে আইন পাঠদান, আইনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা ও প্রকাশনায় নিয়োজিত থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের শিক্ষকদের মধ্যে অনেকে একইসাথে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের তালিকাভুক্ত অ্যাডভোকেট এবং দেশের বিভিন্ন আইনজীবী সমিতির সদস্য। তবে, এই আইনের শিক্ষকদের বৃহত্তর অংশ আদালতে “প্র্যাক্টিশনার” হিসেবে সক্রিয় নন। আইনের শিক্ষকদের অ্যাডভোকেট হিসেবে আদালতে ল প্র্যাকটিস না করার পেছনে কিছু আইনগত প্রতিবন্ধকতা ও মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্ধ রয়েছে- যার পর্যালোচনা জরুরি।
→ বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের Canons of Professional Conduct and Etiquette, 1969 এর ৪র্থ অধ্যায়ের ৮ নং ক্লজ অনুযায়ীঃ
An Advocate should not as a general rule carry on any other profession or business, or be an active partner in or a salaried official or servant in connection with any such profession or business.
এই প্রেক্ষিতে অ্যাডভোকেট হিসেবে তালিকাভুক্ত হওয়ার সময় সব প্রার্থীকে একটি হলফনামা দিয়ে ঘোষণা করতে হয় যে, তিনি কোন ব্যবসা, বাণিজ্য বা চাকুরিতে যুক্ত নেই। পরবর্তীতে অনেক আইনজীবী সমিতি (বার অ্যাসোসিয়েশন) এর গঠনতন্ত্রে সদস্য অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে একই বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি স্পষ্ট যে, উপরোক্ত বিধান-ই আইনের শিক্ষকদের অ্যাডভোকেট হিসেবে আদালতে ল প্র্যাকটিসে প্রধান প্রতিবন্ধক।
কিন্তু ১৯৬৯ সালে প্রণীত পেশাগত আচরণবিধির এই নেগেটিভ ক্লজটি বর্তমান প্রেক্ষাপটে আইনের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে কি না কিংবা এই বিধানের সংশোধন দরকার কি না- তা নিম্নোক্ত কারণে পূনর্মূল্যায়ন করা প্রয়োজনঃ
→ ১৯৬৯ সালে যখন এই বিধানটি প্রণীত হয়েছিল তখন বাংলাদেশ রাষ্ট্রই গঠিত হয়নি। সেসময় দেশে মাত্র দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন শিক্ষা চালু ছিল- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২-বছর মেয়াদি সান্ধ্যকালীন এলএলবি প্রোগ্রাম ছিল। ১৯৭৭-৭৮ সালে এসে চার বছর মেয়াদি এলএলবি (অনার্স) ডিগ্রি চালু হয়। ১৯৯২ সালের আগে এদেশে কোন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির অস্তিত্ব ছিল না। দেশে এখন অনুমোদিত শুধু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১১৫। বাংলাদেশের অধিকাংশ পাবলিক ও প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে বর্তমানে আইন শিক্ষা চালু রয়েছে। সুতরাং, বর্তমান সময়ে এসে ১৯৬৯ সালের উপরোক্ত প্রতিবন্ধকতা ক্লজ এর অন্ধ অনুসরণের সময় আইন শিক্ষার এই বিপুল বিকাশের বাস্তবতা আমাদের বিস্মৃত হলে চলবে না।
→ আইনের শিক্ষকদেরকে “নন-প্র্যাক্টিশনার” ঘোষণা করে আদালত ও আইনজীবীপাড়া থেকে বিযুক্ত রাখলে সেটির সুদূরপ্রসারী প্রভাব চিন্তা করা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের একজন শিক্ষক একইসঙ্গে আদালতে আইন প্র্যাক্টিস করলে তা কি আদৌ “অন্য পেশা” হিসেবে গণ্য হবে, নাকি এটি আইন পেশারই একটি সম্প্রসারিত রূপ, সে বিষয় স্পষ্টীকরণের সময় এসেছে।
→ বিজ্ঞ আইনজীবী এবং বিচারকবৃন্দের কাছ থেকে প্রায়ই এই অভিযোগ শোনা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে আসা আইন স্নাতকদের বাস্তব আদালতের চর্চার সঙ্গে শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের মিল খুবই কম। একদিকে ‘Law in Books’ আর অন্যদিকে ‘Law in Action’-এর মধ্যে ফারাক তৈরি হয়, যার ফলে শিক্ষানবিশ ও নতুন আইনজীবীদের বাস্তব আদালতে মানিয়ে নিতে দীর্ঘ সময় লাগে।
→ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের পাঠ্যক্রম গঠিত হয় মূলত দুই ধরনের আইনের উপর ভিত্তি করে—তাত্ত্বিক (Substantive Law) এবং পদ্ধতিগত (Procedural Law)। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে আইনের ডিগ্রিধারীদের সবাই আইনজীবী পেশায় যায় না- কেউ বিচারক হবে, কেউ শিক্ষক হবে, কেউ আইনের গবেষক হবে, কেউবা অন্য পেশায় যাবে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ শুধুই শিক্ষার্থীকে একজন ‘আইনজীবী’ হিসেবে তৈরি করার ‘ট্রেনিং সেন্টার’ নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের মনে আইনের ধারণার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে দেন। আইন কী?, এটি কীভাবে কাজ করে?, আইন কে কীভাবে বুঝতে হয়?, আইন কীভাবে পড়তে হয়? আইনের গবেষণা কীভাবে করতে হয়? কীভাবে আইনের যুক্তিবোধ (Legal Reasoning) গড়ে তুলতে হয়? -এসব আমরা আইনের শিক্ষকদের কাছে শিখি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের প্রফেসররা আমাদের কে শেখায়- ‘How to think reasonably’। এই শিক্ষা দেওয়ার জন্য আইনের শিক্ষকরাই যথার্থ মানুষ। এই শিক্ষা ছাড়া আইনের চর্চা ত্রুটিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ এবং বিপদজনক।
→ কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের একজন শিক্ষক যার আদালতে আইনজীবী হিসেবে ল প্র্যাকটিসের কোন অভিজ্ঞতা নাই, অথবা বহু বছর আগের প্রায়-বিস্মৃত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন- তাঁর পক্ষে একজন আইনের শিক্ষার্থী কে কি বর্তমান আদালতে আইন প্র্যাকটিসের উপযুক্ত বাস্তব জ্ঞান ও ট্রেনিং প্রদান করে ভবিষ্যৎ আইনজীবী হিসেবে তৈরি করা সম্ভব?
আইন শিক্ষকদের অনেকে প্র্যাক্টিক্যাল জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে আইন পাঠদানের সময় Case Method & Problem-solving Method অনুসরণ করেন না। রিপোর্টেড কেসের বিশ্লেষণভিত্তিক পাঠদান করা হয় না। পদ্ধতিগত আইনসমূহ যেগুলো আইনের বাস্তব প্র্যাকটিসের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত সেসব কোর্স আদালতের সাথে সংযুক্তিহীন, আইনের চর্চা সম্পর্কে প্রায়োগিক অভিজ্ঞতাহীন, শুধু কেতাবি জ্ঞানলব্ধ আইনের শিক্ষকদের পড়ানো কতোটুকু সমীচীন, প্রাসঙ্গিক, কার্যকর ও যুগোপযুগী?
→ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষকদের অনেকে আইন বিষয়ে নিয়মিত গবেষণা করেন এবং তাদের অনেক গবেষণাপত্র আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এসব গবেষণা কি আমাদের আদালতের বিচারক বা আইনজীবীদের কাজে আসে? বরং এগুলো শুধু একাডেমিক চক্রের মধ্যেই ঘুরপাক খায়, যেখানে এক গবেষক আরেক গবেষকের কাজ রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করেন। ফলে, আদালতে গবেষণাধর্মী চিন্তার কার্যকর প্রভাব পড়ে না। এর অন্যতম কারণ হলো, শিক্ষকেরা আদালতে সরাসরি যুক্ত নন এবং আইনজীবীদের প্রয়োজনীয়তার নিরিখে গবেষণা হয় না। ফলে একদিকে আদালত-ভিত্তিক গবেষণা হয় না, অন্যদিকে আদালতের কার্যক্রমেও একাডেমিক গবেষণা তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না।
→ আইন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে বিচারক ও আইনজীবীদের সম্পর্ক বর্তমানে অত্যন্ত আনুষ্ঠানিক, অর্থাৎ, সভা-সেমিনার কিংবা ওয়ার্কশপে এসে লেকচার প্রদান ও ক্রেস্ট বিতরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশে আইন শিক্ষকদের আইনজীবী হিসেবে কার্যকর ভূমিকা পালন করা কিংবা উচ্চ আদালতে আইন প্রফেসরদের ‘Amicus Curiae’ বা আদালতের বন্ধু হিসেবে সংযুক্ত করার প্রচলন অত্যন্ত দুর্লভ। আইনের শিক্ষক ও আইন শিক্ষার্থীদের আদালত, বিচারক ও আইনজীবীদের সাথে সম্পর্কহীন রেখে দক্ষ, যোগ্য “প্র্যাক্টিশনার” গড়ে তোলা কি সম্ভব?
→ এই ব্যবধান কমানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সরাসরি আদালত-সম্পৃক্ত রাখা, যাতে তাঁরা শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে বাস্তব আদালতের চর্চার ধারণা দিতে পারেন। এটিকে বলা হয়- Clinical Legal Education (CLE)। বর্তমানে পৃথিবীজুড়ে আধুনিক আইন শিক্ষার একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ হচ্ছে এই Clinical Legal Education (CLE)।
বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের শিক্ষকদের পাশাপাশি প্র্যাকটিসিং আইনজীবীদেরও পাঠদানে যুক্ত করা দরকার। পদ্ধতিগত আইনসমূহ আইনজীবীরা বা বিচারকেরা পড়াতে পারেন, কারণ তাঁরা সরাসরি এসব আইনের প্রাকটিসে যুক্ত। আবার, যেসব আইন শিক্ষক আদালতে প্র্যাক্টিস করতে চান, তাঁদের উৎসাহিত করা উচিত। এতে শিক্ষার্থীরা কেবল বইয়ের জ্ঞান নয়, আদালতের বাস্তবতাও শিখতে পারবে। বিশ্বের অনেক দেশে এই মডেল অনুসরণ করা হয়, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা আদালতে ল প্র্যাক্টিস করেন এবং অনেক আইনজীবী বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন কোর্স পড়ান। ফলে শিক্ষার্থীরা বাস্তব অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে আসে এবং আইনচর্চায় একটি সেতুবন্ধ তৈরি হয়।
→ অন্যান্য ট্যাকনিকাল এডুকেশন এর ক্ষেত্রে আমরা অ্যাকাডেমিয়া এবং ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে দারুণ কোলাবোরেশান এর চর্চা দেখতে পাই। ফার্মেসি, ইঞ্জিনিয়ারিং, লাইফ সায়েন্সেস, প্রভৃতি। মেডিকেল কলেজের শিক্ষকরা পাঠদানের পাশাপাশি সরাসরি ক্লিনিক্যাল প্র্যাক্টিস ও কনসাল্টেশান করেন, এবং তাদের শিক্ষার্থীরা ক্লাসে তত্ত্বীয় শিক্ষালাভের পাশাপাশি ওয়ার্ডে সরাসরি ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা লাভ করে। আইনশিক্ষাও তো একইভাবে একটি ব্যবহারিক বিদ্যা। কিন্তু আইনের মারপ্যাঁচে ফেলে এই প্র্যাক্টিস থেকে আইন শিক্ষাকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে।
মনে রাখতে হবে, আপনি কেমন “প্র্যাক্টিশনার” হবেন- সেটির ভিত্তি নির্ধারণ করে দেয় আইন শিক্ষা ও আইন শিক্ষকের মান। তাই, আইন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে আইনজীবীদের কোলাবোরেশান, সহযোগিতা ও মিথস্ক্রিয়া বাড়ানোর দিকে নজর দিতে হবে, “নন-প্র্যাক্টিশনার” বিবেচনা করে আইনের শিক্ষকদের সাথে দূরত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে সেটি অর্জিত হবে না।
→ ১৯৬৯ সালের Canons of Professional Conduct and Etiquette এর ৪র্থ অধ্যায়ের ৮ নং ক্লজ এর বিধানটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সেটি “as a general rule”। তার মানে, এটির “exceptional rule” হিসেবে আইন শিক্ষকদের আইন প্র্যাক্টিসে অন্তর্ভুক্তি সম্ভব।
→ ১৯৭২ সালের The Bangladesh Legal Practitioner’s and Bar Council Order, 1972 অনুযায়ী বাংলাদেশের বার কাউন্সিল গঠিত হয়েছে যেটি অ্যাডভোকেট তালিকাভুক্তি এবং লিগ্যাল প্র্যাক্টিশনারদের আচরণ, শৃঙ্খলা ও আইন পেশার মান নিয়ন্ত্রণে একমাত্র বিধিবদ্ধ সংস্থা। এই বার কাউন্সিল অর্ডার এবং রুলস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মানসম্পন্ন আইন শিক্ষা নিশ্চিত করা বার কাউন্সিলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ম্যান্ডেট।
Bar Council Order, 1972 এর Section 10 (i) অনুযায়ী আইন শিক্ষা উন্নীত করা এবং বাংলাদেশে এ ধরনের শিক্ষা প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে পরামর্শক্রমে শিক্ষার মান নির্ধারণ করা বার কাউন্সিলের দায়িত্ব। [to promote legal education and to lay down the standards to such education in consultation with the universities in Bangladesh imparting such education]
Bar Council Order, 1972 এর Section 40 (2) (t) অনুযায়ী- Bar Council may frame Rules providing “the standard of legal education to be observed by universities in Bangladesh and the inspection of universities for that purpose”। অর্থাৎ, বার কাউন্সিল বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কর্তৃক অনুসরণযোগ্য আইন শিক্ষার মান নির্ধারণ এবং এই উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য বিধি প্রণয়ন করতে পারে।
Bar Council Order, 1972 এর Section 11 অনুযায়ী বার কাউন্সিলের যে কয়েকটি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করার কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে Legal Education Committee অন্যতম। এই আইন শিক্ষা কমিটির নয় সদস্যের মধ্যে ন্যুনতম দুইজন বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের আইন শিক্ষক হতে হবে- এমন বাধ্যবাধকতা রয়েছে।
→ গুণগত আইন শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল ২ নভেম্বর ১৯৯৮ তারিখের এক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে Legal Education and Training Institute (LETI) প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যাতে এই ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে এর নতুন তালিকাভুক্ত আইনজীবীদের প্র্যাক্টিক্যাল আইন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা যায়। বার কাউন্সিলের এই উদ্যোগের মাধ্যমে তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক আইন শিক্ষার ব্যবধান কমে আসবে- এমন আশার সঞ্চার হয়েছিল, কিন্তু দুঃখজনকভাবে বর্তমানে এটির কার্যক্রম বন্ধ।
→ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত- সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারিক সিদ্ধান্তেও আইন শিক্ষকদের আদালতে ল প্র্যাক্টিসে সংযুক্ত করার গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা রয়েছে।
Bangladesh Bar Council and Ors v A.K.M. Fazlul Kamir and Ors [14 ADC (2017) 271] মামলায় তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা বার কাউন্সিলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পর্যবেক্ষণ দেন- যদি অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের সরাসরি হাইকোর্ট বিভাগে আইনজীবী হিসেবে অনুশীলনের অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অধ্যাপকগণ, যারা আইন শিক্ষাদানের মাধ্যমে বিচারব্যবস্থার বিকাশে ভূমিকা রাখেন, তাঁদের একই ধরনের সুযোগ দেওয়া হবে না?
প্রধান বিচারপতির নিম্নোক্ত মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য-
If a person holding judicial office is permitted to practice directly in the High Court Division after retirement, why not a professor of law of a university who had taught law students or a high ranking government servant having law degree, who held judicial office (Magistracy) and quashi judicial in his career should not be allowed to practice in the High Court Division in the similar manner of a retired judicial officer. We hope that the Bar Council shall look into the matter and if such categories of persons are permitted, the Bar will be enriched and enlightened. [Judgment, Page 102]
উপরোক্ত পর্যালোচনায় এটি স্পষ্ট যে, আইনের শিক্ষকতা মূলত আইন প্র্যাক্টিসের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং পারষ্পরিক নির্ভরশীল। গুণগত আইন শিক্ষা নিশ্চিত করা বার কাউন্সিলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবং আইন শিক্ষার মানের সাথে প্র্যাক্টিশনারের মান নির্ভর করে। ১৯৬৯ সালের বার কাউন্সিলের পেশাগত আচরণবিধির দোহাই দিয়ে আইনের শিক্ষকদের “নন-প্র্যাক্টিশনার” গণ্য করে যদি বার অ্যাসোসিয়েশন আইন শিক্ষকদের সদস্যপদ বাতিল করে, তবে এটি স্বয়ং বার কাউন্সিল অর্ডার ১৯৭২ এর সাংঘর্ষিক, স্ববিরোধী এবং উচ্চ আদালতের নির্দেশনার ব্যত্যয় হবে। আইন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আইনজীবীদের মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত দূরত্ব সৃষ্টি হবে যা মানসম্মত আইনের গ্র্যাজুয়েট, বিশেষত দক্ষতাসম্পন্ন আইনের প্র্যাক্টিশনার গড়ে তোলার জন্য একটি পশ্চাৎমুখী সিদ্ধান্ত বিবেচিত হবে।
এই প্রেক্ষাপটে, ১৯৬৯ সালের Canons of Professional Conduct and Etiquette এবং সংশ্লিষ্ট বার এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র সংশোধন করার দাবি জানাই। শিক্ষকদের সদস্যপদ বাতিল না করে, বরং বার কাউন্সিলের নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ‘একাডেমিক মেম্বারশিপ’ বা ‘লিমিটেড প্র্যাকটিস মেম্বারশিপ’-এর মতো একটি বিকল্প ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে।
কীভাবে আইন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে আদালত ও আইনজীবীদের সম্পর্ক, সংশ্লেষণ ও সহযোগিতা বাড়ানো যায়, কীভাবে দেশের আইন শিক্ষার মান বাড়ানো যায়, কীভাবে আইনজীবীদের পেশাগত মান, মর্যাদা, সুবিধা ও সুরক্ষার উন্নয়ন করা যায়- আমাদের উচিত বরং সেদিকে মনোযোগ দেওয়া।
লেখক: সাঈদ আহসান খালিদ; সহকারী অধ্যাপক, আইন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
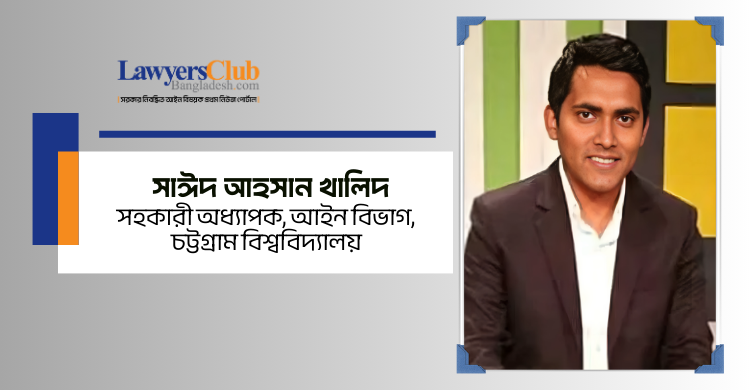
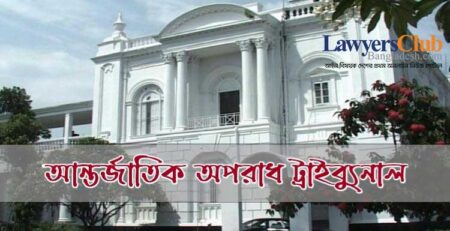
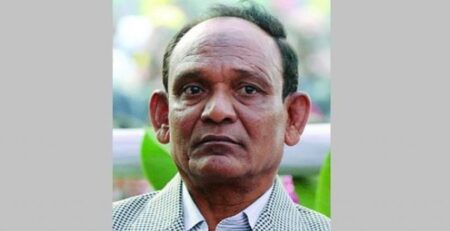
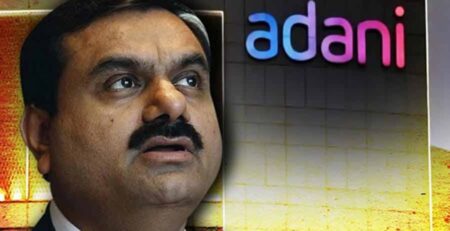





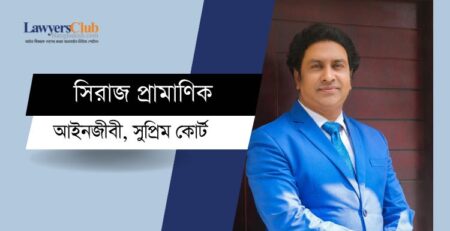

Leave a Reply