চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার আলোকে বিশ্লেষণ
মনজিলা ঝুমা: স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা শুরু হয় নারীর অগ্রণী নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে, যা ইতিহাসে এক সাহসী ও যুগান্তকারী অধ্যায় হয়ে আছে। আমাদের সমাজে নারী নেতৃত্বের নিদর্শন যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে অব্যাহত লিঙ্গ বৈষম্য, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা এবং রাজনৈতিক নিপীড়নের ইতিহাস। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন কেবল একটি প্রতিনিধিত্বমূলক বিষয় নয়, বরং এটি একটি সামাজিক রূপান্তরের কৌশল। আমার লেখায় আমি নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের অগ্রগতি, বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে বিশ্লেষণ করব।
নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, অগ্রগতি ও গৌরবের ধারা
বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক অগ্রযাত্রা একটি সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও সচেতনতার ফল, যার শিকড় আমাদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে প্রোথিত। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে বেগম রোকেয়া নারী জাগরণ ও শিক্ষা আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন, আর প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে নারীর সাহসিকতার নজির স্থাপন করেন। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে হাজারো নারী তাদের জীবন, সম্মান এবং শ্রম দিয়ে অংশগ্রহণ করেন, যারা আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে অবিচ্ছেদ্য অবদান রেখেছেন। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের সংবিধানে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়, যা ছিল একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এরপর ধাপে ধাপে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
২০২৪ সালের জুলাই অভ্যুত্থান (যা বাংলাদেশে একটি রাজনৈতিক মোড় পরিবর্তনের ঘটনা হিসেবে বিবেচিত), তাতে নারীদের ভূমিকা ছিল সাহসিকতাপূর্ণ, সচেতন এবং সংগঠিত। এই অভ্যুত্থানে রাজনৈতিক দমন-পীড়ন, দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন, এবং গণতান্ত্রিক পুনর্দাবির প্রেক্ষাপটে সাধারণ জনগণ রাস্তায় নেমে আসে—নারীরাও এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠেন। ১৯৫২, ৬৯, ৭১, ৯০, ২৪ এর আন্দোলনগুলোতে নারীরা শুধু ‘সহযোগী’ নয়, তারা আন্দোলনের অগ্রভাগে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং সাহসিকতার সঙ্গে প্রতিবাদ ও সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। এসব আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে উঠেছে, যা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনে এক বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। বর্তমানে জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য ৫০টি সংরক্ষিত আসন রয়েছে, যেখানে রাজনৈতিক দলগুলো মনোনয়ন দিয়ে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে। এর পাশাপাশি সাধারণ আসন থেকেও বহু নারী সরাসরি নির্বাচিত হচ্ছেন, যা নারীর রাজনৈতিক সক্ষমতা ও গ্রহণযোগ্যতার পরিচায়ক।
স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাতেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে—ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও জেলা পরিষদে সংরক্ষিত আসনের মাধ্যমে নারীরা এখন grassroots পর্যায়ে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।অনেক নারী সরাসরি সাধারণ আসন থেকেও নির্বাচিত হচ্ছেন, যা তাদের রাজনৈতিক সক্ষমতা ও জনগণের আস্থা প্রদর্শন করে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণ যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও জেলা পরিষদে, যেখানে সংরক্ষিত আসনের পাশাপাশি সাধারণ আসনেও প্রার্থী হচ্ছেন অনেকে। এই পরিবর্তন নারীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সমস্যার সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সাহায্য করছে। গ্রামাঞ্চলে নারীরা পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা চ্যালেঞ্জ করে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং স্থানীয় উন্নয়নে অংশ নিচ্ছেন এটিও একটি পরিবর্তন।
যদিও নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে, তবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধা সত্ত্বেও নারীরা রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে। নারী শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে, বিশেষ করে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে। কর্মজীবী নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তারা প্রশাসন, স্বাস্থ্য, আইন, সাংবাদিকতা, রাজনীতি, এবং তথ্যপ্রযুক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছেন। আইসিটি খাতে নারীদের অংশগ্রহণ এবং উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ড একটি নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। এই প্রেক্ষাপটে একটি নতুন, আত্মবিশ্বাসী ও যোগ্য নারী নেতৃত্বের প্রজন্ম গড়ে উঠছে—যারা নেতৃত্ব দিতে আগ্রহী এবং প্রস্তুত।
তবে প্রশ্ন থেকে যায়: এই অগ্রগতি কতটা অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর? কেবলমাত্র কোটাভিত্তিক অংশগ্রহণ দিয়ে কি নারীরা তাদের বাস্তব ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে পারছে? কোটাভিত্তিক অংশগ্রহণ নারীদের রাজনৈতিক উপস্থিতি নিশ্চিত করলেও, তা কি যথেষ্ট ক্ষমতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ এবং নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাদের প্রকৃত ক্ষমতায়ন ঘটাতে পারছে? নারীর রাজনৈতিক অগ্রগতিকে টেকসই ও কার্যকর করতে হলে কেবল সংখ্যা নয়, বরং গুণগত উন্নয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতায়নকেই মুখ্য করে তুলতে হবে।
নারী নেতৃত্ব, দৃষ্টান্ত ও ক্ষমতায়নের বাস্তব চিত্র
আমাদের সমাজে নারী নেতৃত্বের কিছু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে, যা নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণার উৎস। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পর্যায়ে কিছু নারী নিজেদের কর্মদক্ষতা, দূরদর্শিতা ও নেতৃত্বগুণের মাধ্যমে সফলভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং দিচ্ছেনও। তারা সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের পথে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। তবে এই অগ্রগতির পাশাপাশি বাস্তবতা হলো—এখনও বাংলাদেশের অধিকাংশ নারী লিঙ্গ বৈষম্য, সামাজিক কুসংস্কার, পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব এবং রাজনৈতিক নিপীড়নের মুখোমুখি হয়ে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে চলছেন। রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর সম্পৃক্ততা এখনও অনেকাংশে প্রতীকী, যা শুধুমাত্র কোটা ভিত্তিক উপস্থিতিতে সীমাবদ্ধ থেকে যায়। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন কেবলমাত্র একটি আসনে বসে থাকা নয়—এটি সমাজে কাঠামোগত পরিবর্তন আনার, বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ভাঙার, এবং নারী-পুরুষ সমতার ভিত্তিতে ন্যায়ের সমাজ প্রতিষ্ঠার একটি কার্যকর মাধ্যম। প্রকৃত ক্ষমতায়ন তখনই সম্ভব, যখন নারীরা শুধু প্রতিনিধিত্বই করবেন না, বরং নীতিনির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রেও সমানভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারবেন।
রাজনীতিতে নারীর চ্যালেঞ্জ: কাঠামোগত ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা
বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ক্রমেই বাড়ছে, তবে এই পথচলা এখনো সুগম নয়। নারীরা একদিকে যেমন নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, অন্যদিকে নানা কাঠামোগত ও মানসিক প্রতিবন্ধকতায় প্রতিনিয়ত বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে পুরুষতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামো। দেশের মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলো এখনো পুরুষ-প্রধান মানসিকতা দ্বারা পরিচালিত হয়, যেখানে নারীদের প্রান্তিক ভূমিকায় রাখা হয়। অনেক সময় দলীয় মনোনয়ন, কমিটি গঠন বা গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারণী আলোচনায় নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ সীমিত রাখা হয়। রাজনীতিতে যারা দীর্ঘদিন কাজ করছেন তারাও অনেক সময় মুখ খুলতে ভয় পান, কারণ দলের ভেতরের শ্রেণিবিন্যাস ও ক্ষমতার ভারসাম্য পুরুষদের পক্ষে ভারী থাকে।
এছাড়া রাজনীতিতে পেশিশক্তি ও কালো টাকার প্রভাব নারীর জন্য আরেকটি বড় বাধা। মনোনয়ন পাওয়ার পর মাঠে প্রচারে নামতেই নারী প্রার্থীদের নানা হুমকি ও বাধার মুখে পড়তে হয়। টাকার অভাব, সংগঠনের অভাব, এমনকি সমাজের উপহাস—সব মিলিয়ে একজন নারীকে বহু গুণ বেশি সংগ্রাম করতে হয়। নির্বাচনী রাজনীতিতে যেভাবে টাকা ও সন্ত্রাসের প্রভাব বেড়েছে, তাতে নারী প্রার্থীরা অনেক সময় নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন, যার ফলে তারা মনোনয়ন পেলেও মাঠে দৃশ্যমান হতে পারেন না।
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ধর্মীয় ও সামাজিক গোঁড়ামি। বিশেষ করে গ্রামীণ ও পশ্চাৎপদ অঞ্চলে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে ধর্মীয় ব্যাখ্যা বা কুসংস্কারের মাধ্যমে নিরুৎসাহিত করা হয়। সভা-সমাবেশে নারীর উপস্থিতি, মাইক হাতে প্রচারণা চালানো, বা পুরুষদের সঙ্গে নেতৃত্ব ভাগাভাগি করাকে এখনো নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা হয়। এর ফলে নারীরা নিজেরাও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন, এবং রাজনৈতিক স্বপ্নকে বিসর্জন দেন।
সবশেষে, পারিবারিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা নারীর রাজনৈতিক পথচলায় আরেকটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় নারীর পরিবার—বিশেষ করে স্বামী, পিতা বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা রাজনীতিকে নিরাপদ পেশা মনে করেন না। নারীর নিরাপত্তা, চরিত্র হননের আশঙ্কা, কিংবা দীর্ঘ সময় পরিবার থেকে দূরে থাকার কারণে তারা রাজনৈতিক ক্যারিয়ারকে নিরুৎসাহিত করেন। তাছাড়া, রাজনীতিতে সহিংসতা, মানহানিমূলক প্রচার, এবং সামাজিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন হওয়ার ভয় নারীর মনে এক ধরনের মানসিক প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে, যা তাদের অনেক সময় রাজনীতিতে প্রবেশ করতে নিরুৎসাহিত করে।
এই সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রয়োজন নারী-সহায়ক রাজনৈতিক সংস্কৃতি, নীতিগত সমর্থন, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং পরিবারের সহযোগিতা। কেবলমাত্র সংরক্ষিত আসন নয়, নারীর জন্য প্রয়োজন একটি সহনশীল, নিরাপদ এবং সমান সুযোগের রাজনৈতিক পরিবেশ, যেখানে তারা আত্মবিশ্বাস নিয়ে নেতৃত্ব দিতে পারবেন।
নীতিগত সুপারিশ ও সহায়ক পরিবেশ গঠনের করণীয় নির্দেশনা
বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে টেকসই ও কার্যকর করতে হলে কেবল সংরক্ষিত আসনের নির্দিষ্ট সংখ্যা নির্ধারণ করাই যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন নীতিগত ও কাঠামোগত সংস্কার।
প্রথমত, রাজনৈতিক দলগুলোতে নারীর প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলা এবং বাস্তবায়নের আন্তরিকতা থাকা অত্যন্ত জরুরি। নারীদের শুধুমাত্র কোটাভিত্তিক প্রতিনিধিত্বে সীমাবদ্ধ না রেখে দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাঠামোতে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য দলের গঠনতন্ত্রে নারীবান্ধব নীতি, যেমন—নির্দিষ্ট সংখ্যক নারীকে নেতৃত্বের পদে রাখা, মনোনয়নে প্রাধান্য দেওয়া ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। দলের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ও নেতৃত্ব বিকাশের প্রক্রিয়ায় নারীদের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।
দ্বিতীয়ত, রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ নিরাপদ করতে কঠোর আইন প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা জরুরি। নারীরা মাঠে রাজনৈতিক প্রচারে গেলে হুমকি, যৌন হয়রানি বা সহিংসতার শিকার হন—এমন বাস্তবতা অনেক সময় তাদের অংশগ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করে। তাই রাজনৈতিক সহিংসতা এবং নারীর প্রতি হয়রানির বিরুদ্ধে কঠোর আইন থাকা এবং সেগুলোর যথাযথ প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। নারী প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা, নির্বাচনী প্রচারণা ও ভোটকেন্দ্রে নিরাপদ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সমন্বিত পদক্ষেপ প্রয়োজন।
তৃতীয়ত, নারীদের রাজনৈতিক ক্যারিয়ার গড়তে অর্থনৈতিক সহায়তা এবং প্রশিক্ষণমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। অনেক যোগ্য নারী শুধুমাত্র আর্থিক অসচ্ছলতা বা নির্বাচনী ব্যয় সামাল দিতে না পারায় রাজনীতিতে এগিয়ে যেতে পারেন না। এজন্য নির্বাচনী তহবিল, ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং, রাজনৈতিক কৌশল ও নেতৃত্ব বিকাশমূলক প্রশিক্ষণ চালু করা যেতে পারে। এসব কার্যক্রম স্থানীয় সরকার, ইউএনডিপি, এনজিও বা আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব।
চতুর্থত, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা দরকার। গণমাধ্যম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সক্রিয় ভূমিকা এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। পাঠ্যপুস্তকে নারীর রাজনৈতিক ভূমিকা ও ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করা, নাটক ও ডকুমেন্টারির মাধ্যমে নারীর নেতৃত্বগুণ তুলে ধরা, গণমাধ্যমে সফল নারী রাজনীতিবিদের গল্প প্রচার—এসব উদ্যোগ তরুণ সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নারী নেতৃত্বকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে শিখবে এবং সমাজে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরি হবে।
সামগ্রিকভাবে, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন একটি সামষ্টিক প্রচেষ্টা—যেখানে রাজনৈতিক সদিচ্ছা, নিরাপদ পরিবেশ, অর্থনৈতিক সহায়তা এবং সচেতন সামাজিক কাঠামো একে অপরের পরিপূরক হয়ে কাজ করতে হবে। কেবলমাত্র সংখ্যা বৃদ্ধিতে নয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর কার্যকর অংশগ্রহণই হবে নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়নের সূচক।
পরিশেষে, রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ একটি মৌলিক মানবাধিকার এবং গণতন্ত্রের শক্তি। নারীরা শুধুমাত্র রাজনীতির আঙিনায় নয়, বরং সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃত্বে সমানভাবে অবদান রাখতে সক্ষম। যদিও অনেক অগ্রগতি হয়েছে, তবে নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে প্রয়োজন কার্যকর নীতিগত সংস্কার ও সহায়ক পরিবেশ। বাংলাদেশের নারী নেতৃত্ব একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, যেখানে নারীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমান অংশীদার হিসেবে কাজ করবে।
লেখক : মনজিলা ঝুমা; আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এবং সংগঠক (দক্ষিনাঞ্চল), জাতীয় নাগরিক পার্টি।
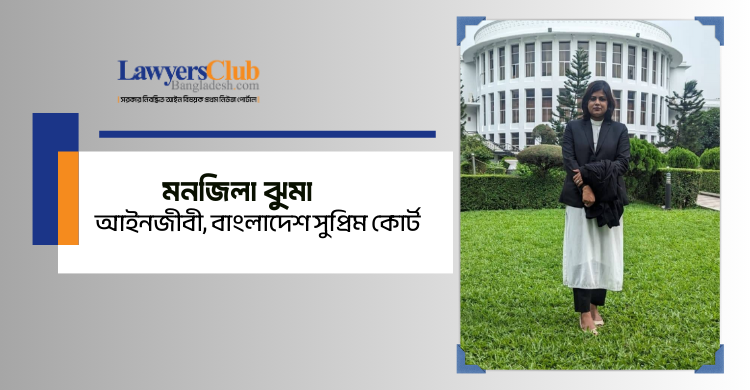








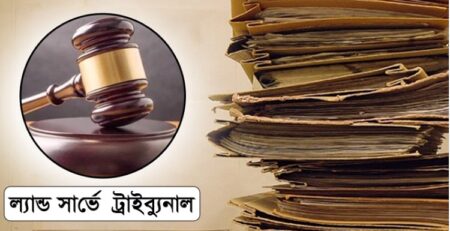

Leave a Reply