বিচার ব্যবস্থা সংস্কারে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার যা হতে পারে
মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম: বিগত ১৬ বছরের দুঃশাসনে আওয়ামী লীগ সরকার বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে এর গ্রহণযোগ্যতাকে মারাত্মকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করে। বিচার ব্যবস্থা নিয়ে জনমনে নানা আশঙ্কা তৈরি হয়। যেমন, আদালতে ন্যায় বিচার না পাওয়া বা বিচার বিলম্বিত হওয়ায় বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের আস্থা একবারে তলানিতে ঠেকে। বিশেষ করে মিথ্যা ও হয়রানিমূলক নাশকতা মামলায় অতিষ্ঠ এই দেশের সিংহভাগ মানুষ। মামলাজটে ও হাসফাস করছে সমগ্র বিচারভিাগ।বিচারক, আইনজীবী, আইন কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সুষ্ঠুভাবে ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের আইনী ব্যবস্থায় বা বিচার বিভাগে ব্যাপক পরিবর্তন ও সংস্কার এখন সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।
বিচার বিভাগ বলতে দেশের সকল শ্রেণী ও পর্যায়ের বিচার ও আদালত ব্যবস্থাকে বোঝায়। উচ্চ আদালত, অধস্তন আদালত, নির্বাহী হাকিম দিয়ে পরিচালিত ভ্রাম্যমান আদালত ইত্যাদি। একজন সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে অধস্তন আদালতের বিচারক হিসেবে কঠিন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা সফলভাবে অতিক্রম করার মাধ্যমে নিয়োগ পান। তদুপরি, অধস্তন আদালতে বিচার বিভাগীয় পদের জন্য আবেদন করার জন্য কিছু যোগ্যতা থাকা লাগে। যেমন- আইনের ডিগ্রি (এলএলবি, এলএলএম) যদি নির্দিষ্ট স্তরের একাডেমিক অর্জন না থাকে তবে কেউ বিচারক হতে আবেদন করতে পারেন না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত উচ্চতর বিচার বিভাগে প্রবেশের জন্য একাডেমিক যোগ্যতার কোনো নির্ধারিত স্তর এবং কোনো ফিল্টারিং সিস্টেম বা পরীক্ষা নেই।
সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের অবশ্যই আইন ও ভাষায় দক্ষ, অভিজ্ঞ, নিরপেক্ষ, সৎ এবং সাহসী হতে হবে। কিন্তু এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগ বিগত বছরগুলোতে সম্পূর্ণ দলীয় বিবেচনায় হয়েছে এবং নিয়োগ দানের জন্য কোন আইন বা পরীক্ষার নিয়ম করা হয়নি।উচ্চ আদালতে বিচারকদের অপসারণের জন্যও বিদ্যমান কোন সুনির্দিষ্ট আইন বা বিধি বিধান নেই। কাউকে দুর্নীতির অভিযোগে বিচারিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা এবং কেউ কেউ রাজনৈতিক বন্ধন বজায় রেখে বিচার কাজ করছেনে।এর ফলে দলীয় বিবেচনায় নিয়োগকৃত বিচারকগণ সঠিক বিচার না করায় সরকারের পতনের পরে পালানোর চেষ্টা করেন বা কেউ কেউ পালিয়েছেন।বিচারকগণ ন্যায় বিচার নিশ্চিত করে বিচার কাজ সমাধা করবেন এটাই অনুমিত।কিন্তু বিগত বছর গুলোতে এমনটি প্রত্যক্ষ করা যায়নি।
আরও পড়ুন: বিচার বিভাগ সংস্কারে ‘ইয়াং জাজেস ফর জুডিশিয়াল রিফর্মের’ ১২ দফা প্রস্তাব
অধস্তন আদালতের বিচারক এবং ম্যাজিস্ট্রেটগণ, জেলা ও দায়রা জজ ও চীফ জুডিসিয়াল/মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রটে এর সার্বক্ষণিক নিয়ন্ত্রণে থাকেন। উক্ত বিচারক এবং ম্যাজিস্ট্রেটগণ দোষী হলে তাদের বিরুদ্ধে জেলা ও দায়রা জজ ও চীফ জুডিসিয়াল/মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রটে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেন। তাছাড়া জেলা ও দায়রা জজ তাদের সকলের কর্মক্ষমতা, যোগ্যতা এবং সততা সম্পর্কে বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন হাইকোর্ট বিভাগে প্রেরণ করেন। অধিকন্তু হাইকোর্টের বিচারকরা নিম্ন আদালত পরিদর্শন করেন এবং তাদের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে আপীল এবং পুনর্বিবেচনা (রিভিউ) নিষ্পত্তি করার সময় সংশ্লিষ্ট বিচারক/ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।
যদিও সংবিধানের ১৬তম সংশোধনীর বহুল আলোচিত রায়ের আগে সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল ছিল যার একমাত্র কাজ ছিল সুপ্রিম কোর্টের কোনো বিচারপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে তদন্ত করা কিন্তু তাদের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার সুযোগ খুব কম ছিল। তবে সামপ্রতিক বছর গুলোতে রাজনৈতিক ও স্বজনপ্রীতি বিবেচনায করায় সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মূল প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবে পরিহার করা হয়েছে।
এই ধরনের পরিস্থিতির পরিণতি হিসাবে যা ঘটতে পারে এই বিষয়ে একজন সাবেক জেলা জজ মর্তুজা মজুমদার স্যার তার ফেসবুকে লিখেছেন,
ক) অধস্থন আদালত ও উচ্চ আদালতের বিচারকদের মধ্যে যোগ্যতার স্তরে ভারসাম্যহীনতা বিরাজ করছে।
খ. কাজের গতি ধীর হয়ে যায় এবং এইভাবে নিষ্পত্তির পরিমাণ কম থাকে।
গ. বিচারে যুক্তি, ন্যায্যতা এবং সমতা নেই।
ঘ) মামলাকারীরা তাদের মৌলিক অধিকার ভোগ করতে ব্যর্থ হয়।
ঙ) অনিয়ম ও দুর্নীতির জন্ম হয়।
চ) আদালতের রায়গুলি প্রায়শই উপেক্ষা করা হয়।
ছ) মানুষ বিচার বিভাগের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছে।
জ. ফলে মানুষ একদিকে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়, অন্যদিকে অন্যায় ও নৈরাজ্য বিরাজ করে।
জনগণ অভিযোগ করে যে সাম্প্রতিক অতীতে সুপ্রিম জুডিসিয়ারির কিছু বিচারক কোনো বা সামান্য জবাবদিহিতা না থাকার কারণে কোনো কাজ না করেই বেতন পান এবং অন্য সব সুবিধা ভোগ করেন। জনগণের বক্তব্য অনুসারে এমন উদাহরণ রয়েছে যেখানে অত্যন্ত জরুরী বিষয়গুলিকে দীর্ঘ তারিখে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল, নিরপরাধ ব্যক্তিদের যথাযথ কারণ ছাড়াই জামিন প্রত্যাখ্যান করে জেল হেফাজতে রাখা হয়েছিল এবং এমনকি পর্যাপ্ত প্রমাণ বা যথাযথ প্রমাণ ছাড়াই দীর্ঘ মেয়াদে দোষী সাব্যস্ত এবং সাজা হয়েছিল। প্রমাণ বা নিছক শ্রবণ এবং অনুমানের ভিত্তিতে। এইভাবে ন্যায়বিচার আশাহীনভাবে ব্যর্থ হয় এবং অন্যায় রাজত্ব করে।
বিচার বিভাগকে আধুনিক, কার্যকরী, স্বাধীন ও শক্তিশালী করার জন্য নিম্নোক্ত সংস্কার এর আহ্বান জানাচ্ছি:
১. অধস্থন আদালতের ন্যায় উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগেও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা চালু করা। হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকদের একটি কঠিন প্রতিযোগীতামূলক লিখিত পরীক্ষার পাশাপাশি ভাইভা ভোসির মাধ্যমে সৎ, দক্ষ ও যোগ্যদের নিয়োগ দিতে হবে।
২. বিচার বিভাগীয় জবাবদিহিতা/জুডিসিয়াল ট্রান্সপারেন্সি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করতঃ ন্যায়বিচার-প্রশাসন দেখতে, ন্যায়বিচার-প্রদান সংক্রান্ত জনগণের অভিযোগগুলিকে বিবেচনা করার জন্য অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র বিচারপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং সুশীল সমাজের সদস্যদের সমন্বয়ে ‘জুডিসিয়াল ট্রান্সপারেন্সি কাউন্সিল’ বা ‘বিচারিক জবাবদিহি কাউন্সিল’ নামে একটি স্বাধীন কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এবং বিচার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বিচার এবং যথাযথ সুপারিশ প্রদানের যথাযথতা নিশ্চিত করা।
৩. জামিনের তাৎক্ষণিক শুনানি- জামিনের আবেদনের শুনানি এবং নিষ্পত্তি করা উচিত তার দাখিলের দিনে বা পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে যেহেতু স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার বিষয়টি মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন জড়িত। কোন নিরপরাধী যাতে এক ঘন্টার জন্যও বন্দী বা কারাবাস না হয় তা নিশ্চিত করা অপরিহার্য।
৪. উচ্চ আদালতে নতুন প্রবেশকারীদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি প্রাথমিক প্রশিক্ষণ কোর্স করা উচিত এবং উপযুক্ত ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে অধস্থন আদালতের বিচারকদের ন্যায়।
৫. শুনানির তারিখ ঠিক করায় আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থিদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান করা দরকার। সুপ্রীম কোর্টে মামলাগুলি শুনানির তালিকায় আসে না যদি না শুনানির তারিখ নির্ধারণের জন্য আনুষ্ঠানিক তারখি ‘মেনশন’ করা হয়। এই বিধানটি বাতিল করা উচিত এবং মেনশন এর জন্য অপেক্ষা না করে আদালতের নিজের দ্বারা শুনানির তারিখ নির্ধারণ করা উচিত।
আরও পড়ুন: বিচারক ও তাঁর পরিবারের সম্পদের হিসাব চেয়েছে সরকার
৬. সার্কিট বেঞ্চ স্খাপন জরুরী। বেশিরভাগ লোকই প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করে এবং অতটা সলভেন্ট না হওয়ার কারণে সর্বোচ্চ আদালতে ত্রাণ চাইতে ঢাকায় আসতে পারে না। জনগণ যাতে সর্বোচ্চ আদালতে সহজে প্রবেশ করতে পারে তার জন্য বিভাগীয় সদর দফতরে হাইকোর্ট বিভাগের সার্কিট বেঞ্চ থাকতে হবে।
৭. প্রধান বিচারপতি যদি প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় উন্নয়নমূলক কাজে সিংহভাগ সময় ব্যয় করেন তাহলে তা বিচার বিভাগের জন্য আরও কল্যাণকর হবে। তিনি শুধু অতি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা সাংবিধানিক ব্যাখ্যার গুরুতর প্রশ্ন জড়িত এমন বিষয়ে আদালতে শুনানির জন্য বসতে পারেন। প্রধান বিচারপতির পরিবর্তে আপিল বিভাগে যুক্তরাজ্যের মতো একজন রাষ্ট্রপতি থাকতে পারেন।
৮. বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি এখন সময়ের দাবী।বিলম্বিত বিচার হল ন্যায়বিচার অস্বীকার করা। তাই বিচার দ্রুত করার জন্য মামলার সংখ্যার অনুপাতে বিচারকের সংখ্যা বাড়াতে হবে।
৯. মামলাজট বিচার বিভাগের জন্য এখন অভিশ্বাপ।অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজদের মামলার বিশাল ব্যাকলগ ক্লিয়ার করার জন্য চুক্তিতে নিয়োগ করা যেতে পারে।
১০. মাসদার হোসেন মামলার নির্দেশনা প্রতিপালনে আরও যত্নবান হতে হবে।বিচার বিভাগের মান ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য মাসদার হোসেন মামলার নির্দেশাবলীকে আর বিলম্ব না করে কার্যকর করতে হবে।
১১. মর্যাদা (স্টাটাস) কেস পর্যালোচনা করে অন্যান্য সার্ভিস এর অফিসারদের মতো বিচারকদের আবাসন সুবিধা, গাড়ির লোন নগদায়নের বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে।বিচারকদের যথাযথ মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং সমস্ত সংশ্লিষ্ট তাত্ক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত যাতে স্ট্যাটাস রায়ের উপর পেন্ডেন্ট রিভিউ পিটিশন নিষ্পত্তি করা যায়।
আরও পড়ুন: বিচার বিভাগের পুনর্গঠন ও সংস্কারে সাবেক বিচারকদের ১২ দফা প্রস্তাবনা
১২. জেলা বিচার আদালতের বিচারকদের নিয়ন্ত্রণে অর্থাৎ পদোন্নতি, বদলি ও ছুটির ক্ষেত্রে আইন মন্ত্রণালয়ের কর্তৃত্ব খর্ব করে হাইকোর্টের উপর ন্যাস্ত করতে হবে।সেজন্য হাইকোর্ট বিভাগের অধীনে পৃথক সচিবালয় চালু করতে হবে।
১৩. বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে নিজেদের বাজেট প্রণয়ন করবে। সেক্ষেত্রে কোর্ট ফিস, আদালত কর্তৃক জরিমানা থেকে প্রাপ্ত টাকা একত্রিত করে বিচার বিভাগের ফান্ডে জমা হবে এবং সেখান থেকে বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে তাদের বাজেট প্রণয়ন করতে হবে।
১৪. আইন মন্ত্রণালয়ের ড্রাফটিং উইং এ আমলার পরিবর্তে বিচারকদের পদায়ন করতে হবে। কারণ লিগ্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডের লোক ছাড়া একটি আইন সুষ্ঠুভাবে ড্রাফট করা সম্ভব নয়।
১৫. ভ্রাম্যমান আদালত (মোবাইল কোর্ট)এর ক্ষমতা কমিয়ে সমান্তরাল বিচার ব্যবস্থা যাতে না প্রতিষ্ঠা লাভ করে সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। জনগণের আকাঙ্ক্ষা মোবাইল কোর্টের জেল প্রদান করার ক্ষমতা থাকা উচিত নয় যাতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হয় বা সমান্তরাল বিচার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে এমন কিছু থাকা উচিত নয়। ন্যায্য ও গুণগত বিচারের জন্য বিচারিক মনের প্রয়োগ একটি অপরিহার্য বিষয়। স্পষ্টতই অভিযুক্তদের কারাগারে রাখার ক্ষেত্রে নির্বাহীদের কার্যনির্বাহী মন প্রয়োগ করার কথা যেখানে অভিযুক্তদের বিচার করা এবং তাদের দ্বারা কারারুদ্ধ করা অনিরাপদ। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে শুধু জরিমানা আরোপের ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে এবং কারাদণ্ডের ক্ষমতা তুলে নেওয়া উচিত।
১৬. জনগণ সর্বোচ্চ আদালতের কাঠামো সম্পর্কে খুবই বিভ্রান্ত। কোনটি সুপ্রিম কোর্ট, কোনটি আপিল বিভাগ এবং কোনটি হাইকোর্ট বা হাইকোর্ট বিভাগ তা বোঝা তাদের পক্ষে কঠিন। সুতরাং আপিল বিভাগের জায়গায় একটি স্বাধীন সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্ট বিভাগের জায়গায় স্বাধীন হাইকোর্ট থাকা আমাদের জন্য ভাল।
আরও পড়ুন: অন্তর্বর্তী সরকারকে আইনজীবী ফেডারেশনের ১৩ দফা প্রস্তাব
১৭. হাইকোর্টের জন্য একজন প্রধান বিচারপতি থাকা উচিত। আপিল বিভাগে বিভাগের জন্য একজন রাষ্ট্রপতিও থাকতে পারেন যিনি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির অনুপস্থিতিতে আদালতের সভাপতিত্ব করবেন এবং পরিচালনার ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।
১৮. জেলা ও দায়রা জজদের নতুন করে নিয়োগ না দিয়ে হাইকোর্টের বিচারক হিসেবে পদোন্নতি দেওয়া হতে পারে যদি কোনো সাংবিধানিক জটিলতা সৃষ্টি না হয়।
১৯. প্রসিকিউশন সার্ভিস গঠন করে পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি), গভর্নমেন্ট প্লিডার (জিপি) এবং অ্যাটর্নি জেনারেলের নিয়োগের জন্য একটি পৃথক প্রসিকিউশন সার্ভিস গঠন করা যেতে পারে যার মধ্যে তার অতিরিক্ত, ডেপুটি এবং সহকারী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে এই ধরনের নিয়োগের জন্য অবশ্যই নির্ধারিত নিয়ম থাকতে হবে।
২০. আলাদা নিরাপদ হেফাজত করা সময়ের দাবী।বর্তমান ব্যবস্থায় বিচারাধীন আসামিদের কার্যত নির্দোষ বা ছোটখাটো অপরাধের জন্য জেলে রাখা হয় যা উক্ত ব্যক্তিদের জন্য খুবই অন্যায্য এবং অসম্মানজনক। একবার একজন ব্যক্তিকে কারাগারে ঢোকানোর পর-সামাজিকভাবে দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং বিচারাধীন আসামিদের রাখার জন্য একটি পৃথক সেফ কাস্টোডি/জুডিশিয়াল কাস্টডি থাকা উচিত এবং এই ধরনের হেফাজত অবশ্যই জেল থেকে দূরে থাকতে হবে এবং ভিন্ন আকৃতি ও পরিবেশের হওয়া উচিত।
লেখক: মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম, আইন গবেষক (পিএউচডি ফেলো) এবং কলামিস্ট।



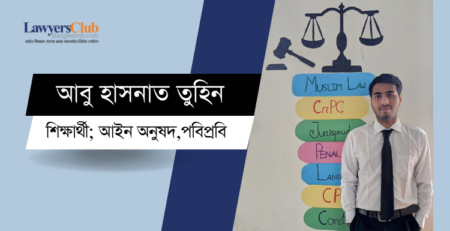

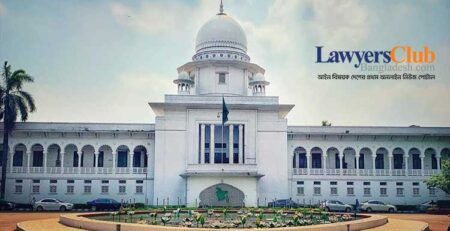




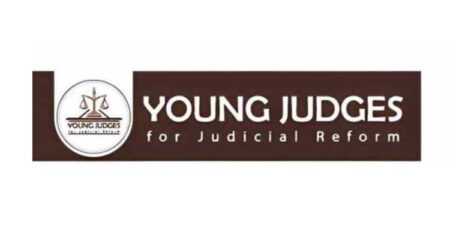
Leave a Reply